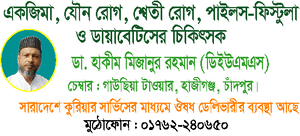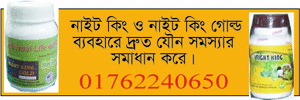
তথ্যপ্রযুক্তি কণ্ঠ ডেস্ক :
ইন্টারনেটের বিস্তার আমাদের জীবনে যেমন অগণিত সুযোগ এনে দিয়েছে, তেমনি কিছু অন্ধকার দিকও উন্মোচিত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো অনলাইন বুলিং—একটি নীরব অথচ ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি। এটি শুধু ব্যক্তিগত মানসিক ক্ষতি করে না, বরং সমাজে একটি বিষাক্ত সংস্কৃতির জন্ম দেয়, যেখানে অপমান, হেয় করা, এবং নিপীড়নকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়।

এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠে—অনলাইন বুলিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কি সাহসের পরিচয়, নাকি নিছক বোকামি? কেউ কেউ বলেন, এতে সময় নষ্ট হয়, কারণ ভার্চুয়াল জগতে অন্যায়ের প্রতিবাদে বাস্তবিক ফল আসে না। আবার কেউ বলেন, প্রতিবাদই পরিবর্তনের প্রথম ধাপ। এই ফিচারে আমরা এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করব, বাস্তব অভিজ্ঞতা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে।
অনলাইন বুলিং: সংজ্ঞা ও প্রভাব
অনলাইন বুলিং বলতে বোঝায় ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কাউকে উদ্দেশ্য করে অপমানজনক মন্তব্য, হুমকি, গুজব ছড়ানো, ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করা, কিংবা মানসিকভাবে আঘাত করার মতো কার্যকলাপ। এটি হতে পারে ব্যক্তিগত আক্রমণ, গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিদ্বেষ, কিংবা নিছক মজা করার নামে কাউকে হেয় করা।
এই ধরনের নিপীড়নের শিকার ব্যক্তিরা প্রায়ই মানসিক অবসাদ, আত্মবিশ্বাসের অভাব, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতায় ভোগেন। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ভয়াবহ হতে পারে। অনেক সময় তারা পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে বিষয়টি ভাগ করে নিতে পারে না, ফলে একাকীত্ব আরও গভীর হয়।
প্রতিবাদ: সাহসের প্রতীক
অনলাইন বুলিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নিঃসন্দেহে একটি সাহসী পদক্ষেপ। কারণ, ভার্চুয়াল জগতে প্রতিবাদ মানে নিজেকে প্রকাশ করা, নিজের অবস্থান স্পষ্ট করা, এবং কখনও কখনও আরও বড় আক্রমণের মুখোমুখি হওয়া। তবু যারা প্রতিবাদ করেন, তারা একটি বার্তা দেন—আমি চুপ করে থাকব না।
এই সাহসিকতা শুধু ব্যক্তিগত নয়, এটি সামাজিকও। একজনের প্রতিবাদ অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে। যেমন, কেউ যদি নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, “আমি অনলাইন বুলিংয়ের শিকার হয়েছি, কিন্তু আমি চুপ থাকিনি,” তাহলে অন্যরাও সাহস পান নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে। এতে একটি সমবেত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।
অনেক সময় প্রতিবাদ সামাজিক আন্দোলনের রূপ নেয়। #MeToo আন্দোলন, #StopBullyingNow—এই ধরনের প্রচারণা মূলত ব্যক্তিগত প্রতিবাদের সমষ্টি। এগুলো সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করে, নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং আইনি পদক্ষেপের পথ খুলে দেয়।
বোকামি: বাস্তবতা না বুঝে আবেগে ভেসে যাওয়া?
তবে প্রতিবাদকে অনেকেই বোকামি বলে মনে করেন। তাদের যুক্তি—অনলাইন বুলিংয়ের জগতে প্রতিবাদ করলে উল্টো আরও আক্রমণের শিকার হতে হয়। অনেক সময় বুলিদের দলবদ্ধ প্রতিক্রিয়া, ট্রল, কিংবা মিথ্যা অভিযোগে ভুক্তভোগী আরও বিপদে পড়ে। ফলে তারা বলেন, “চুপ থাকাই ভালো।”
এই দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে রয়েছে আত্মরক্ষা এবং বাস্তবতাবোধ। কেউ কেউ মনে করেন, ভার্চুয়াল জগতে যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো যায় না, কারণ অনেকেই সেখানে আসে শুধু মজা করার জন্য, কিংবা নিজের হতাশা অন্যের ওপর ঝাড়ার জন্য। ফলে প্রতিবাদ করলে তারা আরও উসকে ওঠে।
তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘমেয়াদে সমস্যাকে আরও গভীর করে। চুপ থাকার সংস্কৃতি বুলিদের উৎসাহ দেয়। তারা বুঝে যায়, “কেউ কিছু বলবে না,” ফলে তারা আরও নির্দ্বিধায় নিপীড়ন চালায়। তাই বোকামি নয়, বরং কৌশলগত প্রতিবাদই হতে পারে সঠিক পথ।
সময় নষ্ট: ফলহীন যুদ্ধ?
আরেকটি সাধারণ মত হলো—অনলাইন বুলিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সময় নষ্ট। কারণ, এতে বাস্তবিক কোনো পরিবর্তন আসে না, বরং মানসিক চাপ বাড়ে। কেউ কেউ বলেন, “ভালো কাজ করো, নেতিবাচকতাকে পাত্তা দিও না।” এই দৃষ্টিভঙ্গি আত্মোন্নয়নমূলক হলেও সমস্যাকে উপেক্ষা করে।
তবে সময় নষ্ট কি না, তা নির্ভর করে প্রতিবাদের ধরন ও উদ্দেশ্যের ওপর। যদি কেউ যুক্তিহীনভাবে প্রতিক্রিয়া দেন, তাহলে তা হয়তো সময় নষ্ট। কিন্তু যদি কেউ সচেতনভাবে, তথ্যভিত্তিকভাবে, এবং সম্মানজনক ভাষায় প্রতিবাদ করেন, তাহলে তা সময়ের সঠিক ব্যবহার।
এছাড়া, প্রতিবাদ মানে শুধু মন্তব্য করা নয়। এটি হতে পারে রিপোর্ট করা, স্ক্রিনশট সংরক্ষণ করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া, কিংবা কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে মানসিক সহায়তা নেওয়া। এইসব পদক্ষেপ সময়সাপেক্ষ হলেও ফলদায়ক।
সমাধানের পথ: প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, এবং পুনর্গঠন
অনলাইন বুলিংয়ের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে কয়েকটি স্তরে কাজ করতে হবে:
১. ব্যক্তিগত সচেতনতা: নিজের মানসিক দৃঢ়তা গড়ে তোলা, আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা, এবং প্রয়োজন হলে সহায়তা চাওয়া।
২. সামাজিক সংহতি: যারা বুলিংয়ের শিকার হন, তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের অভিজ্ঞতা শুনে সহানুভূতি প্রকাশ করা।
৩. আইনি পদক্ষেপ: বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রয়েছে, যা অনলাইন নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ দেয়। সচেতনভাবে এই আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
৪. শিক্ষা ও সচেতনতা: স্কুল, কলেজ, এবং কর্মস্থলে অনলাইন নিরাপত্তা ও সম্মানজনক আচরণ নিয়ে আলোচনা করা জরুরি।
৫. প্রযুক্তিগত সহায়তা: সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে রিপোর্টিং সিস্টেম, ব্লক অপশন, এবং প্রাইভেসি সেটিংস ব্যবহার করা।
অনলাইন বুলিং একটি বাস্তব সমস্যা, যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সাহসের পরিচয়। তবে সেই প্রতিবাদ হতে হবে কৌশলগত, সম্মানজনক, এবং তথ্যভিত্তিক। বোকামি নয়, বরং সচেতনতা ও সংহতির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সময় নষ্ট নয়, বরং সময়ের সঠিক ব্যবহারই পারে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে।
আমরা যদি চুপ থাকি, তাহলে অন্যায় আরও বাড়বে। কিন্তু যদি সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করি, তাহলে অনলাইন জগৎও হতে পারে একটি নিরাপদ, সম্মানজনক, এবং সহানুভূতিশীল স্থান। সাহসী হোন, সচেতন হোন, এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান—কারণ পরিবর্তন শুরু হয় একটি কণ্ঠস্বর থেকেই।
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫