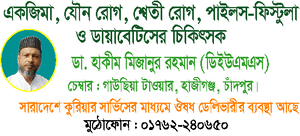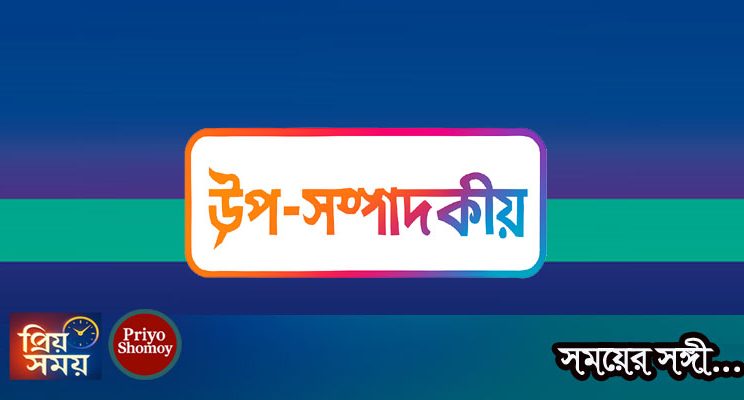
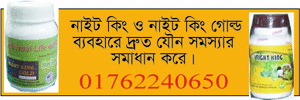
বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশে তরুণদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। এই প্রবণতা শুধু আইনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি নয়, বরং সমাজের ভবিষ্যতের জন্যও এক গভীর সংকেত। তরুণরা জাতির ভবিষ্যৎ, তাদের হাতে গড়ে ওঠে আগামী দিনের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি। কিন্তু যখন এই শক্তিশালী অংশটি অপরাধের পথে পা বাড়ায়, তখন তা শুধু ব্যক্তিগত বিপর্যয় নয়, বরং একটি বৃহৎ সামাজিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। এই ফিচারে আমরা বিশ্লেষণ করবো—কেন তরুণরা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, এর পেছনের মনস্তত্ত্ব, সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং সম্ভাব্য প্রতিকার।
১. পারিবারিক কাঠামোর ভাঙন ও অভিভাবকত্বের সংকট

তরুণদের অপরাধে জড়িয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো পারিবারিক কাঠামোর দুর্বলতা। অনেক পরিবারে বাবা-মা কর্মব্যস্ত, সন্তানদের জন্য সময় নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মা আলাদা হয়ে গেছেন, সন্তান বেড়ে উঠছে একক অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে। এই পরিস্থিতিতে সন্তানরা ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে শেখে না, অভিভাবকত্বের অভাব তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যায়।
পারিবারিক সহিংসতা, অবহেলা, অতিরিক্ত শাসন কিংবা অতিরিক্ত স্বাধীনতা—সবই তরুণদের মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, ভালোবাসা ও স্বীকৃতির খোঁজে অপরাধী চক্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে।
২. সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা
বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তরুণদের বড় একটি অংশ বেকার। উচ্চশিক্ষা শেষ করেও চাকরি না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, সমাজে ধনী-গরিবের ব্যবধান দিন দিন বাড়ছে। তরুণরা দেখে, কিছু মানুষ অল্প সময়ে বিপুল অর্থ, ক্ষমতা ও প্রভাব অর্জন করছে—প্রায়শই অনৈতিক পথে। এই বাস্তবতা তরুণদের মনে এক ধরনের ক্ষোভ ও ঈর্ষা তৈরি করে। তারা ভাবে, “আমিও যদি shortcut পথে যাই, তাহলে দ্রুত সফল হতে পারবো।”
এই মনোভাবই অনেক সময় তাদেরকে অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়—চুরি, ছিনতাই, মাদক ব্যবসা, সাইবার অপরাধ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি।
৩. প্রযুক্তির অপব্যবহার ও ভার্চুয়াল অপরাধ
তরুণরা প্রযুক্তিতে দক্ষ, কিন্তু সেই দক্ষতা সবসময় ইতিবাচক কাজে ব্যবহার হয় না। ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া—এইসব প্ল্যাটফর্মে অপরাধের সুযোগও তৈরি হয়েছে। সাইবার বুলিং, হ্যাকিং, পর্নোগ্রাফি, ডিজিটাল চাঁদাবাজি, ভুয়া আইডি ব্যবহার করে প্রতারণা—এসব অপরাধে তরুণদের জড়িত থাকার হার বাড়ছে।
তরুণদের অনেকেই ভার্চুয়াল জগতে এতটাই ডুবে যায় যে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা ভার্চুয়াল পরিচয়ে আত্মতৃপ্তি খোঁজে, এবং সেই পরিচয় ধরে রাখতে গিয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।
৪. মাদক ও নেশাজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা
মাদক এখন তরুণদের হাতের নাগালে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি পাড়া-মহল্লায়ও মাদক সহজলভ্য। ইয়াবা, গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন—এসব নেশা তরুণদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। তারা হয়ে পড়ে আগ্রাসী, নিয়ন্ত্রণহীন, এবং অপরাধপ্রবণ।
মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়া তরুণদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তারা প্রথমে ব্যবহারকারী, পরে হয়ে ওঠে সরবরাহকারী। এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন, কারণ এতে অর্থ, ক্ষমতা ও ভয় জড়িয়ে থাকে।
৫. রাজনৈতিক ব্যবহার ও অপরাধের পৃষ্ঠপোষকতা
বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় তরুণদের ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। মিছিল, মিটিং, সংঘর্ষ, দখল, চাঁদাবাজি—এসব কাজে তরুণদের ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় রাজনৈতিক নেতারা তাদের অপরাধকে আড়াল করেন, পৃষ্ঠপোষকতা দেন। ফলে তরুণরা অপরাধ করে পার পেয়ে যায়, এবং অপরাধকে ‘স্বাভাবিক’ বলে ধরে নেয়।
এই রাজনৈতিক ব্যবহার তরুণদের নৈতিকতা ধ্বংস করে দেয়। তারা ভাবে, “ক্ষমতা থাকলে সবকিছু করা যায়।” এই মনোভাবই অপরাধকে উৎসাহিত করে।
৬. শিক্ষার সংকট ও মূল্যবোধের অবক্ষয়
শিক্ষা শুধু ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যম নয়, এটি মূল্যবোধ গঠনের হাতিয়ার। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা শেখানো হয় না। তরুণরা পরীক্ষার নম্বর, চাকরির প্রস্তুতি, প্রতিযোগিতায় এতটাই ব্যস্ত যে তারা মানুষ হওয়ার শিক্ষা পায় না।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহিংসতা, দলাদলি, রাজনৈতিক প্রভাব—এসব তরুণদের মনে বিভ্রান্তি তৈরি করে। তারা বুঝতে পারে না, কোনটা সঠিক, কোনটা ভুল। এই বিভ্রান্তিই অপরাধের জন্ম দেয়।
৭. মিডিয়া ও বিনোদনের প্রভাব
টেলিভিশন, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, ইউটিউব—এসব মাধ্যমে অপরাধকে রোমান্টিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। একজন গ্যাংস্টারকে ‘হিরো’ বানিয়ে দেখানো হয়, একজন প্রতারককে ‘চতুর’ বলে প্রশংসা করা হয়। তরুণরা এসব দেখে প্রভাবিত হয়। তারা ভাবে, “অপরাধ করলে আমি জনপ্রিয় হবো, ভয়ংকর হবো, সবাই আমাকে সম্মান করবে।”
এই বিকৃত চেতনা তরুণদের অপরাধের দিকে টেনে নেয়। তারা বাস্তবতা ভুলে যায়, এবং ফ্যান্টাসির জগতে ঢুকে পড়ে।
৮. মানসিক স্বাস্থ্য ও পরিচয় সংকট
তরুণদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা বাড়ছে—হতাশা, উদ্বেগ, আত্মবিশ্বাসের অভাব, পরিচয় সংকট। তারা বুঝতে পারে না, কে তারা, কী চায়, কোথায় যাচ্ছে। এই সংকট তাদেরকে আত্মবিনাশের দিকে নিয়ে যায়।
অনেক তরুণ অপরাধ করে শুধু নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য। তারা চায়, কেউ তাকে দেখুক, চিনুক, ভয় পাক। এই মনোভাবই অপরাধকে জন্ম দেয়।
৯. বন্ধুত্ব, প্রেম ও সম্পর্কের জটিলতা
তরুণদের জীবনে সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু যখন সম্পর্ক ভেঙে যায়, বন্ধুত্বে বিশ্বাসভঙ্গ ঘটে, প্রেমে প্রতারণা হয়—তখন তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক সময় প্রতিশোধের আগুনে অপরাধ করে বসে।
সম্পর্কের জটিলতা, সামাজিক চাপ, সম্মান রক্ষার নামে সহিংসতা—এসব তরুণদের অপরাধে জড়িয়ে ফেলে।
১০. আইনের দুর্বল প্রয়োগ ও বিচারহীনতা
যখন অপরাধ করে কেউ পার পেয়ে যায়, তখন অপরাধ বাড়ে। তরুণরা দেখে, অপরাধ করে কেউ শাস্তি পায় না, বরং ক্ষমতা, অর্থ, পরিচয় দিয়ে সবকিছু ম্যানেজ করে। এই বিচারহীনতা তরুণদের মনে অপরাধের প্রতি এক ধরনের ‘স্বাভাবিকতা’ তৈরি করে।
তারা ভাবে, “আমিও পার পেয়ে যাবো।” এই বিশ্বাসই অপরাধকে উৎসাহিত করে।
সমাধানের পথ
তরুণদের অপরাধ প্রবণতা কমাতে হলে সমাজের প্রতিটি স্তরে পরিবর্তন আনতে হবে। শুধু আইন দিয়ে নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে তরুণদের পাশে দাঁড়াতে হবে।
১. পরিবারে ভালোবাসা, সময় ও নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে
২. শিক্ষায় মানবিকতা, সহমর্মিতা ও মূল্যবোধের চর্চা বাড়াতে হবে
৩. মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে
৪. প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার শেখাতে হবে
৫. আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে
৬. রাজনৈতিকভাবে তরুণদের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে
৭. মিডিয়ায় অপরাধের রোমান্টিক উপস্থাপন বন্ধ করতে হবে
৮. তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ বাড়াতে হবে
৯. সম্পর্ক ও বন্ধুত্বে সহনশীলতা শেখাতে হবে
১০. সমাজে ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে
তরুণরা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, কারণ তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এই পথ দেখানোর দায়িত্ব আমাদের সবার।